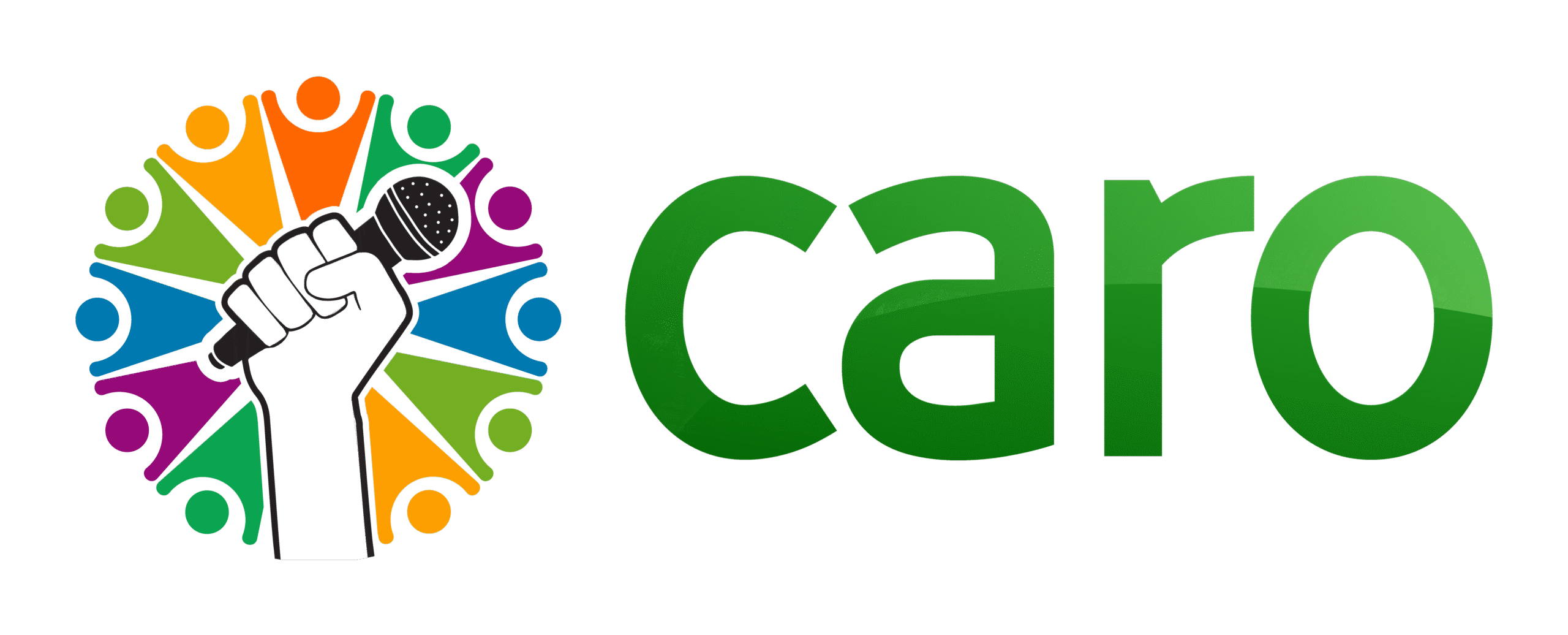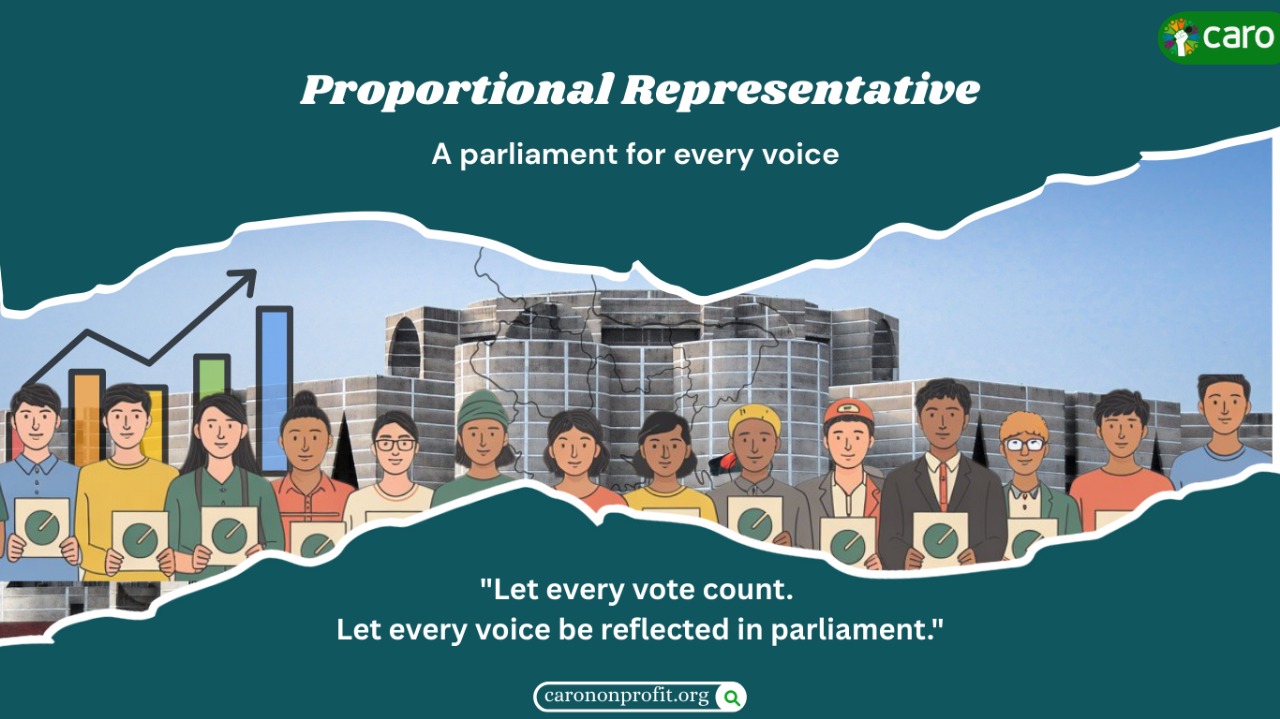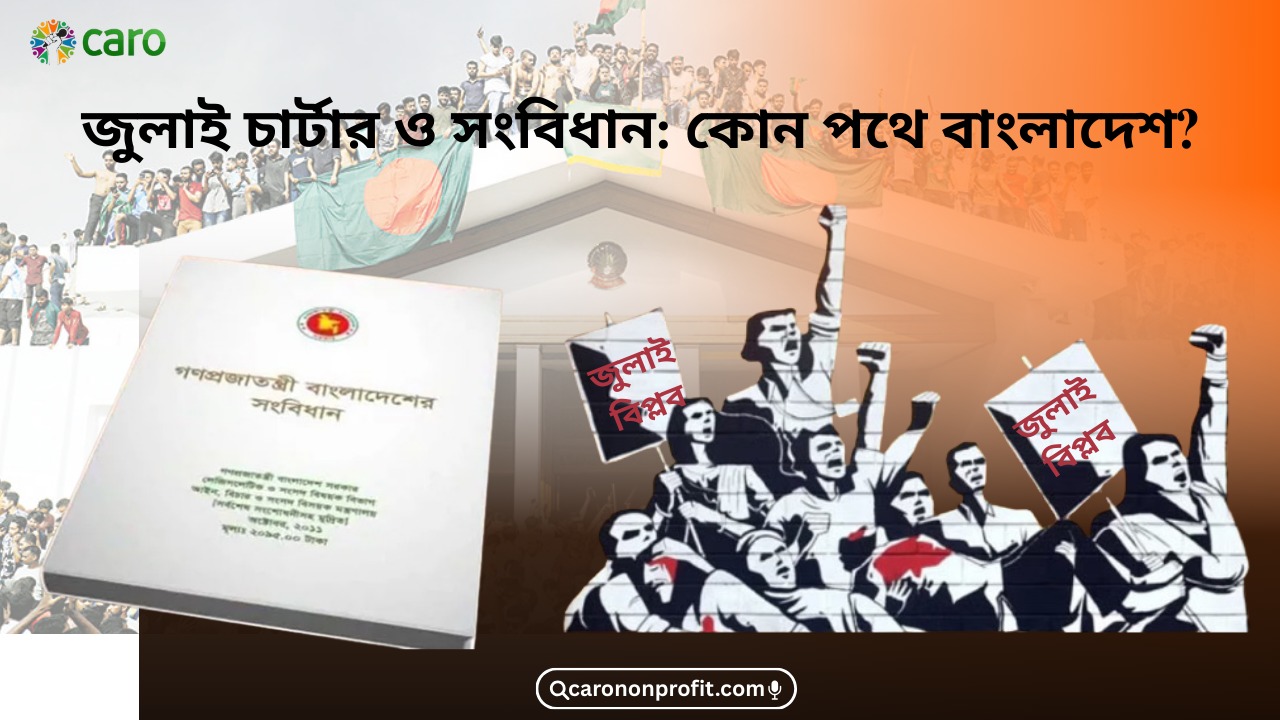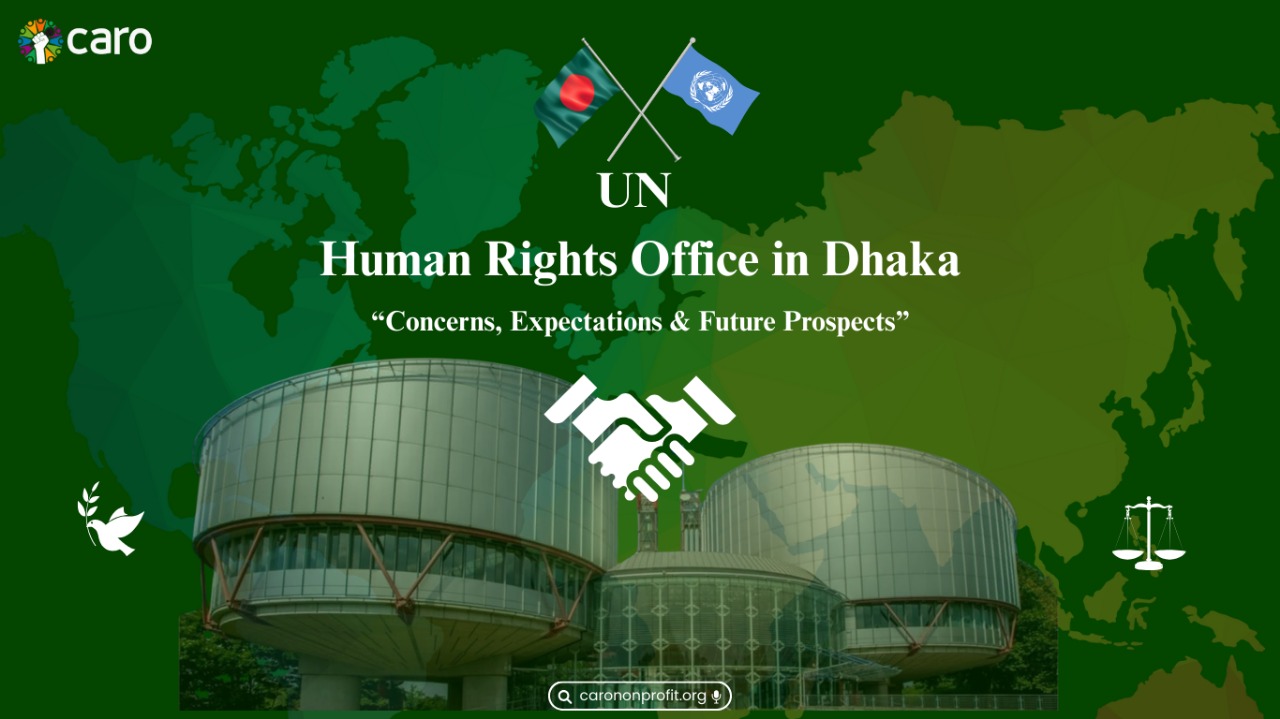কীভাবে একটি রাজনৈতিক দল জাতীয়ভাবে প্রায় ৪১% ভোট পেয়ে মাত্র ১০% এরও কম সংসদীয় আসন পেতে পারে? এই প্রশ্নটি বাংলাদেশের নির্বাচনী ন্যায়বিচারের মূল কেন্দ্রে আঘাত হানে। ভোটের অংশীদারিত্ব ও আসনের মধ্যে এই বিশাল ব্যবধান গণতান্ত্রিক বৈধতাকে দুর্বল করে, জনগণের কণ্ঠকে প্রান্তিক করে এবং রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বিকৃত করে।
বাংলাদেশ বর্তমানে First-Past-The-Post (FPTP) নির্বাচনী পদ্ধতি অনুসরণ করে, যেখানে প্রতিটি আসনে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী বিজয়ী হন—জাতীয়ভাবে একটি দলের মোট ভোট শতাংশ যতই হোক না কেন। যদিও এটি সরল এবং ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত, এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই অন্তর্ভুক্তিমূলক, আনুপাতিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।
এর বিপরীতে, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation – PR) এমন একটি বিকল্প, যেখানে প্রতিটি ভোটের মূল্য থাকে, অংশগ্রহণ উৎসাহিত হয় এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের মতো একটি পরিপক্ক গণতন্ত্রের জন্য এখন সময় এসেছে আত্মসমালোচনা করার—বর্তমান ব্যবস্থা কি সত্যিই জনগণের সেবা করছে, নাকি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠদের আধিপত্য ধরে রাখছে?
১. আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR) কী?
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এমন একটি নির্বাচনী পদ্ধতি, যেখানে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের প্রাপ্ত জাতীয় বা আঞ্চলিক ভোটের অনুপাতে সংসদীয় আসন পায়। বিজয়ীর সবকিছু পাওয়ার (FPTP) বিপরীতে, PR পদ্ধতিতে প্রতিটি ভোটের মূল্য থাকে, এমনকি সংখ্যালঘুদের কণ্ঠও সংসদে প্রতিফলিত হয়।
উদাহরণস্বরূপ, একটি দল যদি ২০% ভোট পায়, তাহলে তারা প্রায় ২০% আসন, অর্থাৎ ৩০০টি আসনের মধ্যে প্রায় ৬০টি আসন পাবে। এইভাবে কোনো ভোট “অপচয়” হয় না এবং প্রতিটি ভোটারের পছন্দ সরকার গঠনে বাস্তব প্রভাব ফেলে।
PR ব্যবস্থা একাধিপত্য রোধ করে, জোট গঠনের প্রবণতা বাড়ায় এবং অধিক সহযোগিতামূলক ও বহুবাদী শাসনব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে।
২. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে PR-এর ধরন ও ব্যবহার
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR) পদ্ধতির একাধিক ধরন রয়েছে, যেগুলো বিশ্বের বিভিন্ন স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সফলভাবে প্রয়োগ হচ্ছে। নীচে এই ধরনগুলো এবং সংশ্লিষ্ট দেশের বাস্তব প্রয়োগ তুলে ধরা হলো:
১. ক্লোজড লিস্ট PR
এই পদ্ধতিতে ভোটাররা প্রার্থী নয়, দলকে ভোট দেন। নির্বাচনের পর দল নিজেই নির্ধারণ করে—তাদের তালিকা অনুযায়ী কারা সংসদে যাবে।
বৈশিষ্ট্য: দলে শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং নির্বাচনী ব্যয় কম হয়, তবে ভোটারের ব্যক্তিগত পছন্দের সুযোগ সীমিত থাকে।
ব্যবহারকারী দেশ:
🔹 দক্ষিণ আফ্রিকা – যেখানে এই পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।
২. ওপেন লিস্ট PR
এই ব্যবস্থায় ভোটাররা শুধু দল নয়, দলের ভেতরের নির্দিষ্ট প্রার্থীকেও নির্বাচন করতে পারেন। এটি নির্বাচনে ভোটারদের অধিক সক্রিয় অংশগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।
বৈশিষ্ট্য: প্রার্থীদের পারফরম্যান্সের ওপর গুরুত্ব পড়ে, এবং ভোটার সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারেন কে সংসদে যাবেন।
ব্যবহারকারী দেশ:
🔹 সুইডেন ও নরওয়ে – যেসব দেশগুলো গণতন্ত্রে স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে এই পদ্ধতিকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে।
৩. মিশ্র-সদস্য আনুপাতিক (MMP)
এটি একটি সংকর পদ্ধতি, যেখানে কিছু আসন সরাসরি ভোটের মাধ্যমে এবং বাকি আসন দলীয় তালিকার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়। এতে ব্যক্তি ও দলের উভয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।
বৈশিষ্ট্য: নির্বাচনের ভারসাম্য বজায় রাখে, শক্তিশালী সংসদীয় কার্যকারিতা ও অংশীদারিত্বমূলক শাসনের পথ তৈরি করে।
ব্যবহারকারী দেশ:
🔹 জার্মানি ও নিউজিল্যান্ড – যারা দীর্ঘদিন ধরে এই মডেল অনুসরণ করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব বজায় রেখেছে।
বৈশ্বিক বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি কোনো পরীক্ষামূলক ধারণা নয়—এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি গণতান্ত্রিক মানদণ্ড।
৯০টিরও বেশি দেশ বর্তমানে কোনো না কোনো ধরনের PR পদ্ধতি অনুসরণ করে।
২০টিরও বেশি OECD দেশ, যেমন জার্মানি, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড, দীর্ঘদিন ধরেই সফলভাবে PR বাস্তবায়ন করছে।
বেলজিয়াম ছিল প্রথম দেশ যারা ১৮৯৯ সালে PR গ্রহণ করে—এরপর থেকে দেশটি রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।
এই বৈশ্বিক বাস্তবতাগুলো স্পষ্ট করে যে PR পদ্ধতি শুধু একটি তাত্ত্বিক ধারণা নয়, বরং গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, ঐকমত্য-ভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক করে তোলার একটি কার্যকর ও পরীক্ষিত উপায়।
৩. বাংলাদেশে PR কেন প্রাসঙ্গিক?
১. ভোট-আসনের বৈষম্য কমানো
FPTP পদ্ধতিতে ভোট ও আসনের ভারসাম্য প্রায়ই ভয়াবহভাবে অসমান।
২০০১: বিএনপি পায় ৪০.৮৬% ভোট, কিন্তু ১৯৩টি আসন। আওয়ামী লীগ পায় ৪০.২২% ভোট, কিন্তু মাত্র ৬২টি আসন।
২০০৮: আওয়ামী লীগ পায় ৪৮.০৪% ভোট, কিন্তু ২৬২টি আসন। বিএনপি পায় ৩২.৫%, কিন্তু মাত্র ৩০টি আসন।
এমন অসামঞ্জস্য গণতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট করে, বড় দলগুলোর আধিপত্য বাড়ায় এবং বিশাল জনগোষ্ঠীকে কার্যত চুপ করিয়ে দেয়। PR এই বৈষম্য দূর করে ভোটের প্রতিফলন আসনে নিশ্চিত করবে।
২. প্রতিটি ভোটের মূল্য নিশ্চিত করা
বর্তমানে একজন প্রার্থী ২৫–৩০% ভোট পেয়েই জিততে পারে। বাকি ৭০–৭৫% ভোট কার্যত “অপচয়” হয়ে যায়। PR এই ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিটি ভোটকে আসনে রূপান্তর করে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সরল উদাহরণ:
ধরুন, জাতীয় সংসদে মোট আসন ৩০০টি। একটি রাজনৈতিক দল ২০% ভোট পেলেও FPTP ব্যবস্থায় তারা কোনো আসনেই সর্বোচ্চ ভোট না পেলে একটিও আসন পাবে না—যদিও তারা প্রায় ৩০–৪০ লাখ ভোট পেয়েছে।
কিন্তু PR ব্যবস্থায় একই দল তাদের ২০% ভোট অনুযায়ী প্রায় ৬০টি আসনে প্রতিনিধিত্ব পেত।
এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ভোট “অপচয়” না হয়ে সংসদে কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিফলিত হয়—এটাই PR পদ্ধতির অন্যতম ন্যায়সঙ্গত দিক।
৩. ছোট দল ও নতুন আন্দোলনের অংশগ্রহণ
বর্তমান FPTP পদ্ধতিতে কোনো রাজনৈতিক দল জাতীয়ভাবে ৫–১৫% ভোট পেলেও যদি তারা কোনো নির্দিষ্ট আসনে সর্বোচ্চ ভোট না পায়, তবে কার্যত কোনো আসনই অর্জন করতে পারে না। এতে করে একটি বৃহৎ ভোটারগোষ্ঠীর মতামত সংসদে প্রতিফলিত হয় না—যা গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ন্যায্যতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি উদাহরণ:
ধরা যাক, কোনো দল ১০% জাতীয় ভোট পেয়েছে—অর্থাৎ প্রায় ৭০–৮০ লাখ মানুষ তাদের ভোট দিয়েছে।
FPTP পদ্ধতিতে, যদি দলটি কোনো আসনে সর্বোচ্চ ভোট না পায়, তাহলে তারা শূন্য আসন পায়—সেই ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব সংসদে অনুপস্থিত থাকে।
PR পদ্ধতিতে, একই পরিমাণ ভোটে দলটি ৩০টি আসন (১০% × ৩০০) পেত, যা তাদের ভোটারদের কণ্ঠস্বর সংসদে যথাযথভাবে তুলে ধরত।
একইভাবে, ১৫% ভোট পেলে FPTP-তে তারা গড়ে ২–৫টি আসনের বেশি পায় না, অথচ PR পদ্ধতিতে সেই দল প্রায় ৪৫টি আসন পেতে পারত।
এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, PR ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক, যা ছোট দল, আঞ্চলিক গোষ্ঠী ও উদীয়মান রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মকে বাস্তব রাজনৈতিক পরিসরে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর ফলে সংসদ আরও বৈচিত্র্যময়, বহুমতসম্মত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে ওঠে।
৪. সামাজিক প্রতিনিধিত্ব ও অন্তর্ভুক্তি
PR পদ্ধতি নারীদের, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের, পেশাজীবী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাজনীতিতে প্রবেশে সহায়ক।
PR ব্যবহারকারী দেশগুলোতে নারী ও সংখ্যালঘু এমপির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে।
৪. PR-এর সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ
১. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব
জোট সরকারে বিভিন্ন দলের সমন্বয় করতে গিয়ে বিলম্ব হয়।
উদাহরণ: ইতালিতে প্রায়শই সরকার পরিবর্তিত হয়।
২. দলীয় কেন্দ্রীকরণ বৃদ্ধি
বিশেষ করে ক্লোজড লিস্টে প্রার্থী নির্বাচন পুরোপুরি দলের হাতে—অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র দুর্বল হতে পারে।
৩. স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অসুবিধা
PR পদ্ধতি দলকেন্দ্রিক হওয়ায় স্বতন্ত্ররা পিছিয়ে পড়ে।
৪. ছোট দলের অতিরিক্ত প্রভাব
জোট গঠনে ছোট দলগুলো কখনও কখনও “কী পার্টি” হয়ে অত্যধিক দাবি আদায় করতে পারে।
উদাহরণ: ইসরায়েলে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর নীতিগত প্রভাব।
৬. উপসংহার
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিখুঁত নয়, কিন্তু এটি বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়সঙ্গত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক।
যেহেতু বাংলাদেশ গভীরতর গণতন্ত্রে রূপ নিতে চায়, রাজনৈতিক বৈধতা নিশ্চিত করতে চায় এবং সমাজের বৈচিত্র্যকে সংসদে তুলে ধরতে চায়—তাই PR আর কেবল বিকল্প নয়, এটি এক অনিবার্য প্রয়োজন।
প্রতিটি ভোট গণ্য হোক।
প্রতিটি কণ্ঠ শুনুক।
প্রতিটি নাগরিক যেন সংসদে নিজেকে খুঁজে পায়।
একটি শক্তিশালী, ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের জন্য, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বই ভবিষ্যতের পথ।
তথ্যসূত্রঃ
১. উইকিপিডিয়া – বাংলাদেশ সাধারণ নির্বাচন ২০০১ ও ২০০৮
২. বিবিসি বাংলা – ড. তফায়েল আহমেদের সাক্ষাৎকার (২০২৪)
৩. OECD ভোটিং ডেটাসেট (২০২৩)
৪. International IDEA – নির্বাচনী ব্যবস্থা ডিজাইন হ্যান্ডবুক
৫. যুগান্তর ও জনকণ্ঠ – নির্বাচন রিপোর্ট (২০২৪–২৫)